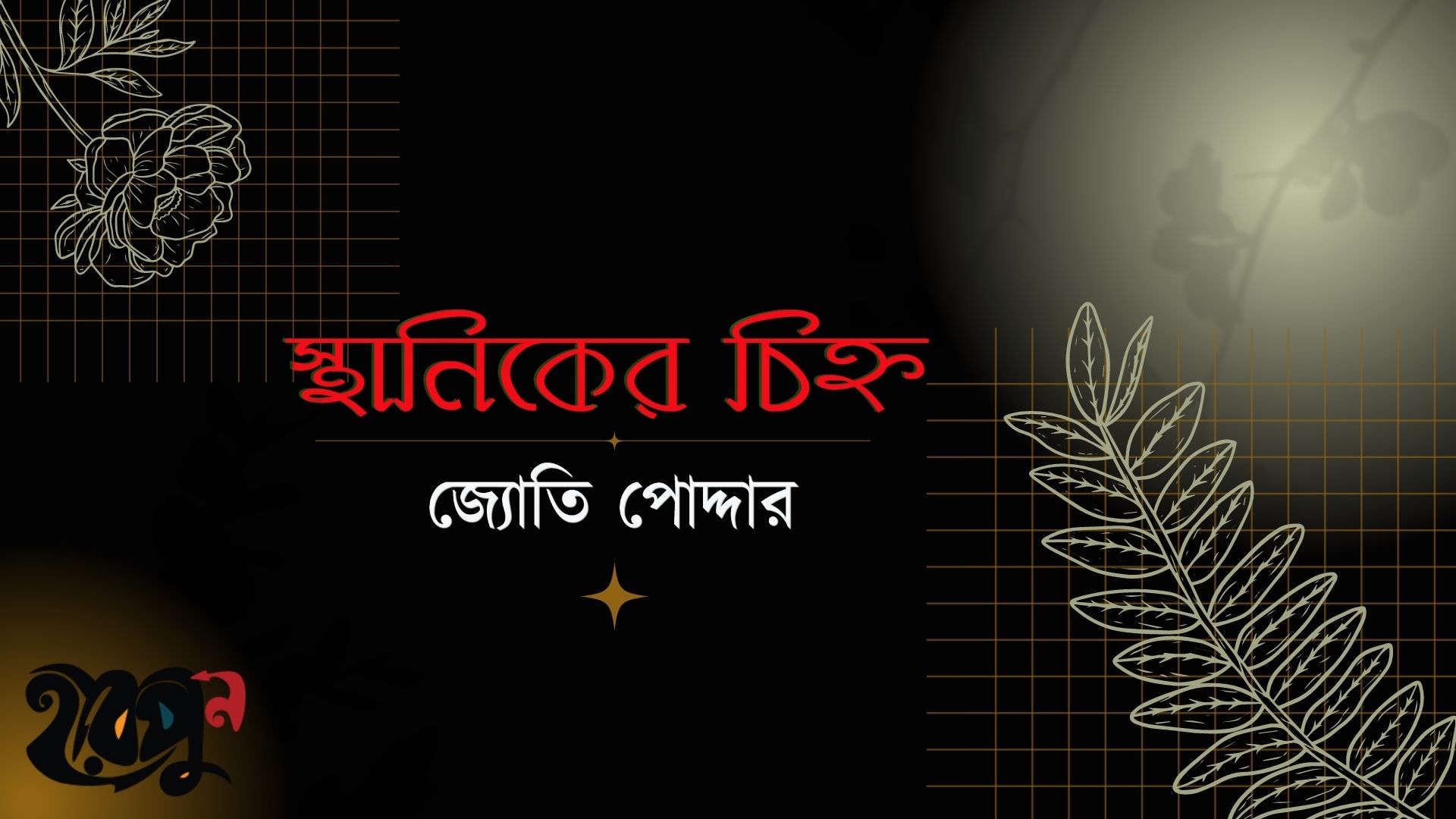স্থানিকের চিহ্ন ।। জ্যোতি পোদ্দার
মিশ্র বৃক্ষের বনে চোখ ক্লান্ত হয় না— বরং ছলকে ছলকে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়লে এমন জায়গা পেলে হাত পা মেলে দেবার জন্য শরীর নেচে ওঠে। মন আকুপাকু করে। যেন কতকাল পর সবুজ আর সবুজ আর ঘন সবুজের মায়াবী বিছানা পেতে রেখেছে আমার জন্য। গা এলিয়ে দিলেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ নীচু হয়ে আমার পাশে বসে চুলে বিলি কেটে কেটে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।
সকালের রোদে পাতার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে যতটুকু আলোর বিস্তার ঠিক ততটুকুই বরফির ছাঁচের মত ছায়া পড়ে নিকানো উঠান জুড়ে। ভারি সুন্দর লাগে আলো ও ছায়ার এমন এক্কাদোক্কা খেলা। ধুলাবালি মেশানো উঠানে পড়ে থাকা পাতার মিছিল মাড়িয়ে পেছন দিকে যেতেই এক অখণ্ড নীরবতা খান খান করে ভেঙে পড়ল হঠাৎ হাত থেকে পড়ে যাওয়া কাঁচের গ্লাসের মতো। শুকনো পাতার এমন কুঁকড়ে ওঠা শব্দকেও তখন ভারী যন্ত্রের ঘর্ষণের মতো কানে বাজে।
অথবা দুয়েকটা স্যাতারে ডেকে উঠলেই বোঝা যায় কী ভীষণ নীরবতার ভেতর ডুবে ছিল এই মাজার প্রাঙ্গণ। পাখির গুঞ্জনে ভেঙে পড়ে সব নীরবতা। সরবতা তখন সমগ্র উঠান জুড়ে একাকী রাজত্ব করে। দীর্ঘ রাজত্ব।
সরবতা থেকে নীরবতার দূরুত্ব যতটুকুই হোক না কেন নীরতার ঘাটে সহজে ভেড়া যায় না—এখানে এখনই হওয়া যায় না। করোটির কোষে কোষে শুধু অতীত আর ভবিষ্যতের রশি টানাটানিতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে। বর্তমানে থাকতে পারি না কোন ভাবেই। এখানে এখনই থাকা মানে সকলের সাথে গাঁটছড়া বেঁথে থাকা। একত্বে থাকা। অভেদের ভেতর থাকা।
বড় রাংটিয়ার বনের ভেতরে এই মাজার। হযরত সেকান্দর আলীর মাজার। চৌচালা রেলিঙ দেয়া ঘরে লালসালু মোড়ানো কবর। নাওয়ের ছইয়ের মতো কবরের চারদিকে সোনালি জড়িবুটি ঝালর ঝুলে আছে। সালুরঙে রঙিন টিনের চেগারে সিমেন্টের খুঁটি আর সিঁড়ির ধাপগুলো কালো রঙ করা। তার নীচে জোতা রেখেই খানকায় ঢুকে ভক্তবৃন্দ। মেঝেতে আধখানা পোড়া মোম ও পুড়ে ফ্যাকাশে ছাই হয়ে পড়ে আছে ধুপকাঠী।
বাঁশের ঝাঁক ঝুঁকে পড়েছে টিনের চালে। মরা পাতায় সয়লাব চৌচালা টিনের চাল। সামনের টুকু পাকা করা। করোনা প্রার্দুভাবের কারণে এইদিকে কেউ আজকাল আসেনা। এমনিতেই এটি সংরক্ষিত বন। মিশ্র বৃক্ষের বিস্তারের কারণে উজ্জ্বলতা ছড়াচ্ছে জায়গাটা।
আজকাল লোক সমাগম কম। মাজার ছাড়িয়ে কিছুদূর এগুলে পরপর কোচ বাড়ি। পাশাপাশি ঘর। লম্বা যৌথ উঠান। উঠানের পাশেই যার যার তুলসি মঞ্চ আর ছোট্ট করে বানানো থান। গৃহ দেবতার ভিটি। সকাল সন্ধ্যায় ফুল জলের পাশে জ্বলে মাটির প্রদীপ। কারো আবার পুড়ে যাওয়া সলতার বুক তেল মেখে পড়ে আছে মাটির মুছিতে।
কী সুন্দর নিকানো উঠান আর ঘরের মেঝে চিরুনি দিয়ে আঁচাড়ানো। অর্ধবৃত্তের মাপে সরু সরু দাগ। খালি পায়ে হাঁটলেই টের পাওয়া যায় কোচ নারীর হাতে লেপা মোছা মাটির কার্পেট। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো মেঝে আর উঠান। পায়ের পাতায় কেমন কেমন যেন অনুভব হয়। ঘরের দেয়াল রোদের আলোয় চকচক করে যেমন তেমনি ঘরের ভেতর শীতলতা মোড়ানো জড়ানো।
এই মাজারে ওরশ হয় ফাগুন মাসে। ঠিক কবে মাজার প্রতিষ্ঠিত তার তত্ত্বতালাশ করে পাওয়া গেলো না। বনের মালিক যে বন বিভাগ তাঁর কাছেও নেই। একেক জনের কাছে একেক তথ্য। কেউ প্রাচীনতা প্রমাণে তৎপর কেউ বলে এই তো সেদিনের কথা।
কেউ আবার পীর কেন্দ্রিক ধারণাকে অস্বীকার করে আবার কেউ বলে চাঁদ দেখিয়ে দেবার জন্য যে আঙুল লাগে সে চাঁদ নয়— নির্দেশক কাঠিমাত্র; এমন প্রযোজক কর্তার দরকার আছে। তেমনি পীর— সেই পরমের সাথে মিলবার ও মেলাবার সেতুমাত্র। যে যেভাবে বলে বলুক। আমার শুনতে ভালোই লাগে। ভিন্নতার অভিমুখ চর্তুমুখী হবার কারণে নানা স্বাদ পাই।
ফাগুনের চান্নিরাতে বসে এই ওরশ। সারারাত চলে জিকির। পরমকে স্মরণ করার জিকির। সদগা হাতে ছুটে আসে নানা জায়গার নানা মানুষ। কেউ আকাঙ্খা করে বা কারো মানত পূর্ন হয়েছে বলে হালের বলদ ডাগর লাল মুরগী নয়া সব্জীর চাল কুমড়ো বা লাউ অথবা যা মুরিদের ইচ্ছে হয় তাই নিয়ে ছুটে আসে পীরের ওসিলায় সেই পরমের কাছে উৎসর্গ করে। তাঁর মনোতুষ্টির জন্য। ছোয়াবের জন্য।
বিশ্বাসে বিশ্বাস রেখে মানুষ তাঁর দিন গুজরান করে। নিজে নিজের পায়ে দাঁড়াবার কসরত না করে কারো না কারো উছিলায় বাঁচে। বাঁচতে চায়। মাজার তেমনই একটি খানকা— একটি আশ্রয়। খেটে খাওয়া মানুষের অবলম্বন। উছিলা। মুরিদের হইজগত যন্ত্রনাময়। কেবলই পাঁকে পাঁকে সে জড়িয়ে পড়ে। তাই সে মরণের পারে কোন এক দূর অলৌকিক জীবনের মন্ত্রনা খোঁজে খোঁজে হয়রান। সেই জীবন যেন একটু শান্তি পায়।
কিন্তু নিত্য চিতার আগুন আর নির্বাপিত হয় না— ক্রমেই বেড়ে চলে উর্ধ্বগতিতে। মানুষের আর মুক্তি মেলা না। জিকিরে জিকিরে জীবন গেলো। স্মরণে স্মরনে দিন রাত গুজরান হলো। তবু অক্টোপাসের অষ্টেপৃষ্ঠে অষ্টাপাশ আর কাটল না খেটে খাওয়া মানুষের।
যাপনের স্টিয়ারিং যারা ঘুরায় নিজেদের স্বার্থে তার চাকায় দাহ হচ্ছে কালের মানুষ। মানুষ তাঁর কাছে স্রেফ উৎপাদনের হাতিয়ার। মুজরি দাস। তার উপায়। অন্যের গতর খাটিয়ে পুঁজি বৃদ্ধি করা তার সাধারণ লক্ষ্য।
সেই লক্ষ্যের জন্যই মানুষের চৈতন্যে ধর্মবোধের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে অর্হনিশি। মুক্তি যেন সেই পরপারে। মানুষের যে জীবন প্রকৃতি দিয়েছে এখানে যেন তাঁর কিছু হবার নয়। কিছুই করার নেই। জন্মান্তরের পাপ ঘানি টানবার জন্য বারবার এই সংসারে ফিরে আশা।
চৈতন্যের সমগ্র এলাকাকে সরু পথ নিয়ে এসে জীবকে আটকে রাখার ফন্দি। যেন নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে না পারে। বিশ্বাসে বিশ্বাসে মাথা ঠুকে কখনো দরগায় কখন সোনা রাঢ আর রূপা রায় থানে কখনো কষ্টিপাথরের মূর্তির পদতলে। না যাজকের না যজমানের কারো জীবনেই মুক্তি ঘটল না। সর্বত্র শুধু যাজক। ছোট বড় যাজক। নানা কায়দা কৌশলে যজমানকে আটকে রাখা। তাঁর তাঁবে রাখা। যাজকে হাতে রয়েছে অস্ত্র ও শস্ত্র। মনকে দাবিয়ে রাখার জন্য শ্রাস্ত্রের ব্যবস্থাপনা আর দেহকে সায়েস্তা করার জন্য নানা কিশিমের অস্ত্রের ঝনঝনানি।
মন্ময়ে তন্ময়তায় স্থাপন করে কেউ আকারবাদী কেউ নিরাকারবাদী। কেউ অদ্বৈতবাদী—সর্ব খলিদং ব্রহ্মা। আবার কেউ দ্বৈতবাদী। তাঁর কাছে তার জগত আমি—সে এর বন্ধনে গ্রন্থিত জগত। নানা মতের মতো নানা পথ। নানা ভক্ত। যে যেমন অধিকারী তেমনি তার ব্যবস্থাপত্র।
তবু দিশা নেই। নিজের মতের ও পথের প্রতি যে ভালোবাসা শ্রদ্ধা সে রাখে ততটুকু ভিন্নমতের ভিন্ন মানুষের পথের প্রতি রাখে না। ভাষার ভেতর কী করে যে ভিন্ন ভিন্ন ভেদ হয়ে থাকে সেটি ভক্তের মালুম হয় না। সেই প্রজ্ঞা তাঁর নাই। সে আট দশটা জিনিষের মতোই সে-ই নিত্যশূন্যকে মনে করে।
যেন ভক্ত যে ভাষায় রাঙিয়েছে সেটাই এক মাত্র উচ্চারণ। অন্যের গুলো অপরিপক্ক শুধু নয় অপরের পথ ভুলভাল পথ। ভাষার ভেতর প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মহাজন। আলাদা আলাদা মোকাম। আর আমরা আলাদা আলাদা মহাজনের আলাদা আলাদা গাহেক।
সেই পরমের স্মরণে এখানে ফাগুন মাসের শুক্লপক্ষের তিথিতে বাউল গানের আসর বসে। তত্ত্বকথা হয়। আলাপে আলাপে গানে গানে যুক্তিখণ্ডন হয়। তন্ময় হয়ে শুনে মায়াভরা চোখে জল নিয়ে বসে থাকা মুরিদ। রাতের পর রাত যায়— ডুগডুগি আর করতাল থামে না। সিন্নি জুড়িয়ে ঠান্ডা হয় মনে তবু নিত্যচিতা। মুক্তির বাসনা। মুক্তি আর মেলে না।
মানুষে মানুষে যে ভেদ এই সমাজব্যবস্থা করে রেখেছে তাকে ঠিক রেখে কি মুক্তি মেলে? মানুষের সাথে মানুষের ও প্রকৃতির সম্পর্কের বিকাশ এই মনুষ্য জন্মেই। এই জীবনের বাইরে মুক্তি সে তো গোলক ধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া।
মানুষের টিকে থাকা শুধু মানুষের জন্য নয়। মানুষের টিকে থাকা নির্ভর করে অন্যান্য প্রাণের টিকে থাকার উপর। মানুষ নিজেই সেই প্রাণ ও প্রকৃতি অংশ। কাজেই নিজের টিকে থাকার লড়াই সংগ্রামের সাথে অন্য প্রাণের টিকে থাকার লড়াই। সেই লড়াই মানুষকেই করতে হয়। করতে হবে। সপ্রানতা আজ হুমকির মুখে। যে মনোভঙ্গি আমাদের যাপন চাবিকাঠি সে মনোভঙ্গি ইগোকেন্দ্রিক ভোগবাদি নিজেকে নিয়ে বাঁচার মনোভঙ্গি। চাই ইকোকেন্দ্রিক সগ্রাণতার পাটাতন-সকলের সাথে সকলের এক মহাজীবনের স্বর ও সুর ভক্ত বিশ্বাসে মশগুল। তর্ক তার কাছে আর গতি পায় না। সমর্পনেই মুক্তি। মাজার ছাড়িয়ে আরেকটু এগুলেই রাধা গোবিন্দ মন্দির। এই ফাগুনেই বসে ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের মেলা। এখানেও সেই পরমকে স্মরণ। নেচে গেয়ে সংকীর্তনের শরণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিজেকে উৎসর্গিত করা। চলে ভোগারতি। চার প্রহরব্যাপী নাম সংকীর্তন। ধুপধুনো আর আলোর ঝালসানো আসর রাধাভাবে আকুল হয়ে সেই পরম কৃষ্ণকে শরণ। ভক্তের হৃদয় উপচিয়ে চোখ ভেসে যায় নামপ্রেমের সাগরের নোনা জলে।
এই মন্দির বেশি দিনের না। বছর বিশেক হবে। এই তল্লাটের সিংহভাগ মানুষই দেশভাগের পর দেশান্তরি। কেউ শহর মুখী। আচিক মান্দিরা শরণ নিয়েছে খ্রিষ্ট্রিয় মতবাদে জেসাসে দুখবোধের সাথে নিজেদের দুখবোধের যন্ত্রণা মিলিয়ে তার পাদপদ্মে উৎসর্গিত এখন গারো জীবন। সেখানেও আচিকরা অখন্ড থাকেনি। ভেদবুদ্ধির চাপে ও চিপায় তারাও তিন ভাগে বিভিক্ত। তবু কয়েকঘর আচিক মান্দি আছে তারা ঘাড়ত্যাড়া করে রয়ে গেছে সাংসারেক ধর্মে।
কোচ বর্মন ডালু হদি—সনাতনে মিশে গেছে। পেছনে রেখে এসেছে তার চর্চিত বিশ্বাস। পরম্পরা জ্ঞান। বর্ণবাদে বিভক্ত সনাতন হিন্দু কোন বর্ণেই তাদের আশ্রয় দেয়নি। সংখ্যা বাড়িয়েছে শুধু। কোচ ডালুরা নিজেকে ক্ষত্রীয় বলেই দাবী করে। মানে লেঠেল জাত। অপরের পেয়াদার। সে-নিয়েও তাঁর গর্বের শেষ নেই। রয়েছে নানা উপকথা। অহংবাদী বয়ান। ক্ষেতের সাথে লেগে থাকা কোচ ডালু বানাই হদিদের যে নিজস্ব ক্ষেত্রতেজ যে উৎপাদকের তেজ তা ভুল গেছে নানা গল্প গাছায়। অপরের লেঠেল হবার বাহানায়। উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন পরম্পরা জ্ঞান এখন শুধুই বিশ্বাস। গল্পকথা।
একদিকে নিজের বর্ণের শ্রেষ্ঠতার গর্বে নিজেই মাতোয়ারা অন্যদিকে অপর বর্ণের প্রতি রয়েছে গোপন ও প্রকাশ্য নিন্দা। জাতিবাদীর এমন বাসনা নিজের বয়ানেই থাকে। অপরকে ছোট করে দেখা। নিজেকে স্বয়ম্ভু হিসেবে দেখা। নিজের তরিকায় শুধু নিজের মুক্তি দেখে না। অপরেরও মু্ক্তি দেখে। অপরের প্রতি হীনতাই তাকে আগ্রাসী পরিচয়বাদীতে রুপান্তর করে।
চৈতন্য নিতাই অদ্বৈতাচর্যে নামে ধ্বনি দিতে দিতে বিগলিত হলেওে চৈতন্যের শিক্ষা নিতাইয়ের শিক্ষা যাপনে আনতে পারেনি সনাতান হিন্দু সমাজ। চৈত্যনের শিক্ষা বর্ণবাদ বিরোধী লিঙ্গবাদ বিরোধী জাতিবাদী বিরোধী শিক্ষা। সেই শিক্ষা যাপনে আনবার বাচনিক মানসিক শারীরিক নিদান চর্চায় আনে নি। গুরুবাদের খপ্পরে সনাতন মূলত বিভাজিত হিন্দু। বর্ণের আর গোত্রের উছিলায় নানা গুরুমুখী পরিচয়বাদী।
সনাতন সমাজ কাঠামোতে তাই উপেক্ষিত থেকে গেছে কোচ বর্মণ রাজবংশি হদি ডালুরা। নিজেদের সমাজ নিজেদের মতো করে পুরোহিত বা গাঁও বুড়ার নেতৃত্বে চলছে তারা। সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ইসকন। চৈত্যন্যের ভক্তিবাদের সাথে বেদবাদ মিশিয়ে যত মতের তত পথের প্রেক্ষিত না রেখে এক পথ এক মতের দিকে মূলত তাদের যাত্রা। যা একান্তভাবে চৈতন্যবিরধী।
এই ইসকনে ভিড়েছে কোচ রাজবংশি হদিও। এই রাংটিয়াও ব্যতিক্রম নয়। ষোল নাম কলির মুক্তি বলে বলে হরে কৃষ্ণ হরে রাম গাইলেই মুক্তি মেলে না। প্রয়োজন অব্যবস্থপনার বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো। মানুষে মানুষে বিভেদের জায়গা চিহ্নিত করে মানুষেকে এক নিজের দুর্দশার কারণ সন্ধান করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার মন্ত্রনা দেয়া। এই বিজ্ঞাপিত পন্যায়িত বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখা।
শুধু স্মরণ করেই অশ্রুজলে বুক ভাসালো। দুখের কারনের কারন নিয়ে ভাবনা যথাযথ ভাবে না ভেবে দুখকে ভাবল পূর্বজন্মের কর্মফল হিসেবে। নিয়ত সংগ্রাম করা মানুষ সময়ের ফেরে “নিয়ত”কে ভাবলো নিয়তিবাদীর খপ্পরে পড়ে— কাপালে যা আছে তাই হবে এমন ভাবনায় মশগুলের ফাঁদে পড়ে।
আলাপটা মাজার নিয়ে হচ্ছিল। কথায় কথায় কথালতা বেড়ে গেলো খানিকটা। কথলতার মতো মাজার প্রাঙ্গণ মূলত লতানো গিলা লতার প্রাঙ্গণ। অনেক খানি উঠান জুড়ে জড়ানো ছড়ানো লতার বিস্তার। সেগুনের আশ্রয়ে তরতর করে বেয়ে ওঠা গিলা লতা এমন ভাবে পেঁচিয়ে আছে যে সেগুনের কান্ড দেখায় যাচ্ছে না। বয়সের ভরে লতা মোটা মোটা রশির মতো হয়ে গেছে। লতার গা খসখসে। মোটা। প্যাঁচানো রশির মতো। কে জানে এই গিলা লতার বয়স কত?
চির সবুজ আশ্চার্য এই গিললতা। লতায় লতায় এই লতা জড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। এক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তার ঘটতে পারে অনায়াসে। এক বৃক্ষের কাণ্ড থেকে আরেক বৃক্ষের কাণ্ডে দ্রুত সংযুক্ত হয়ে পড়ে। গড়ে তুলে লতা ব্রীজ। মাজারের সামনের চাতালে এমন ভাবে লতিয়ে লতিয়ে লতা ব্রীজ তৈরি করেছে যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। মানুষে মানুষে ভেদের এই সময়ে এমন ব্রীজই দরকার। এমন একটি ব্রীজিং রুখে দিতে পারে যে কোন শক্তিকে। পণ্যায়িত বিজ্ঞাপিত ভেদের সমাজ ভাঙতে হলে চাই গিলা লতার মতো জড়ানো ছড়ানো ব্রীজিং।
গিলা ফল আমি দেখেনি। লতার যেমন ঔষুধী গুণ আছে তেমনি গিলা ফলেও। সনাতন সমাজে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান। কী বরের কী কনে— গায়ে হলুদ পর্বে গিলার ব্যবহার হলুদ ধান দূর্বার মতোই প্রয়োজনীয় উপাদান।
বিয়ে সামাজিক শিষ্টাচার। সকলের শুভাশীষে সিক্ত হয় বর কনে। সকলে মিলে নয়া দম্পতির হাতে মুখে পায়ে হলুদ লাগিয়ে দেয়া আর্শিবাদের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। সনাতন সমাজ প্রকৃতি থেকে খুঁজে নেয় তাঁর আর্শিবাদ প্রতীক। দুই হাতে ধান দুর্বা দিয়ে বরকে বরণ করে দেয়া শিষ্টাচারে থাকে বর তুমি ধানের মতো ধনবান হও দূর্বার মতো চিরজীবী। তেমন হলুদ প্রতীকে থাকে দেহের দিক থেকে সুস্থতা আর মনের দিকে থেকে প্রশান্ততা। দেহ ও মন নিয়ে মানুষ। দাম্পত্য তার সুচনা বিন্দু। আর্শিবাদের ঘনঘটা এখানে তাই একটু বেশি।
হলুদ মাঙ্গলিক উপাদান যেমন তেমন প্রাকৃতিক জীবানুনাশকও। হলুদের সাথে গিলা ফল বেটে খোঁচপাচাড়া মতো শারিরীক রোগে নারিকেল তেল মিশিয়ে ব্যবহার একটা সময়ে প্রচলন ছিল।
এই যে লতানো স্বভাবের গিল লতা। নিজের কাছে থাকা যে কোন গাছকেই নিজের মতো জড়িয়ে নেয় আপন স্বভাবে। তাঁর পাশপাশের কোন বৃক্ষকেই সে দূরে রাখে না। নিজের বেষ্টনিতে যোগ করে নেয় সকলকে।
মানুষ হিসেবে আমরা ঝাঁকপ্রানী। সকলকে নিয়ে সকলের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে রয়েছি গিলা লতার মতো— পার্থক্য এই যে খাসিলতের কারণে অপরকে সাথে সংযূক্ত চেতনাকে বেমালুম ভুলে যাই। একার জীবন মানুষের নয়। মানুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি লতা মাত্র। “Man did not weave the web of life; he is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself.”