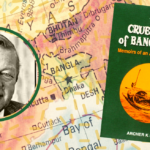ফালগুনী রায়ের কবিতায় সত্তা ও অন্যান্য ডিসকোর্স ।। মমিন মানব ।। ৩য় পর্ব
কবিতামুখ ও ফেয়ার এন্ড লাভলি
পোয়েট্রিফেস নিয়ে ভাবছি। যেখানে একটা ফেস থাকে। আরও পষ্ট করে বললে বলতে হবে যেখানে একটা ফেসবুক থাকবে। এর জন্য বিভিন্ন ফ্রেন্ড হবে, যারা কেউ কাউকে চিনবে না, জানবে না (কিছুটা হয়তো চিনা/জানা থাকবে)। কিন্তু তারা ফেসবুকফ্রেন্ড থেকে বুক (ইংরেজি হলে জ্ঞানাধার; মানে বই। আর বাঙলা ধরলে তো সর্বনাশ, বুক; মানে হৃদযন্ত্র/হৃদয় যেখানে থাকে) বাদ দিয়ে শুধু ফেসফ্রেন্ডই থাকে। সে হিসেবে ফেসবুককালচার (অথবা ফেসকালচার) নিয়ে আমাদের জানাশোনা খারাপ না। ফেসকালচার থেকেই আমাদের ফেসপোয়েট্রি। অথবা পোয়েট্রিফেস। যার বাঙলা দাঁড়াবে কবিতামুখ।
মুখ শব্দটা আমরা মুখ ও মুখমন্ডল দুই অর্থ হিসেবেই ব্যবহার করে থাকি। লেখাটা শুরু করার আগে আমি পোয়েট্রিফেস পোয়েট্রিফেস আওড়ালেও শেষ পযর্ন্ত সেটা কবিতামুখ বাঙলায়নের মাধ্যমেই নামকরন করবো (করতে বাধ্য হবো)। কিন্তু আমরা এখানে মুখ শব্দটাকে মুখ হিসেবেই দেখবো। এবঙ কবিতামুখ ইংরেজিকরন করলে দাঁড়াবে (হয়তো দাঁড়িয়ে লাফ দিবে) পোয়েট্রিমাউথ। পোয়েট্রি এখানে তাই ফেসবুকিয় ফেস (কিংবা অন্য কোনো ফেস) হিসাবে থাকছে না। হয়ে যাচ্ছে মাউথ: যেখানে হলারের (রাইসমিলে ধান সিদ্ধ করার বিরাট পাত্র/ভেসেল) একটা গর্ত থাকে, আবার সেখানে কথা/গান ডেলিভারি দেবার মতোন একটা মাইকও থাকে আবার যেখানে মাউথর্অগান বা বাঁশি ও বাজে। পোয়েট্রিমাউথ বলে লেখার শুরুতেই এভাবে একটা ভয়ানক রকম অকাব্যিক শব্দবন্ধ নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে পাঠক (মানে আপনি যিনি পড়ছেন) হয়তো পেছন থেকে পালাবেন। আমি /আমরা তাই এখানে কবিতামুখ শব্দবন্ধ নিয়েই সামনে হাঁটছি।
(স্যরি,) মুখ শব্দটা নিয়ে আরও একটু বিরক্ত করি। জ্বালামুখ (আগ্নেয়গিরির ক্ষেত্রে কিঙবা চুলার ক্ষেত্রে), দ্বিমুখি সাপ (দুই মাথা/প্রান্ত কিঙবা দ্বিচারিতা অর্থে), র্সূযমুখি এই কবিতামুখের মুখ শব্দের সাথে মিল/সাদৃশ্যতা/সম্পৃক্ততা নেই। জানি না এখানে সূর্যমুখি বলতে সূর্যের মতোন মুখ বুঝানো হয়েছে, নাকি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকা বুঝাইছে) যেটা-ই হোক না কেনো, কোনোটার অর্থই আমাদের আজকের মুখ শব্দের অর্থ না। কারণ র্সূযমুখির প্রথম ব্যাখ্যায় মুখি বলতে মুখমন্ডল আর দ্বিতিয় ব্যাখ্যায় মুখি বলতে মুখাপেক্ষি (কাঙাল কাঙাল ভাব) বুঝানো হয়েছে।
কবিতার সাথে এই মুখ শব্দের আপাতত সর্ম্পক না হাতড়িয়ে এই সব বাড়তি কথার কারন হলো কয়েকদিন আগের এক ঘটনা/দৃশ্য:
ব্যাঙকের কাজে ভিতরে ঢুকতেই ব্যাঙক ম্যানেজার তার এক কলিগকে বলছে, আপনে তো অনেক সুন্দর হয়ে গেছেন; ইদানিঙ খুব ফেয়ার এন্ড লাভলি খান বুঝি!

মূলত ফেয়ার এন্ড লাভলি মুখে (মানে মুখমণ্ডলে) দেয়া মানে জাস্ট মুখে দেয়াই বুঝায় না। মুখে দেয়ার অর্থ এখানে একটা বাহ্যিক/আপাত/অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদ (আমরা কিন্তু এখানে অসমাপিকার ক্রিয়ার কথা চিন্তা করে মূল বিষয় থেকে ভিন্ন পথে সড়ে যাবো না)। কেনো এটা অসম্পূর্ণ! দিব্যি তো সম্পূর্ন। কবিতা তার মুখে হলুদ দিচ্ছে। কবিতা তার মুখে সাবান দিচ্ছে। কবিতা তার মুখে পেট্রোলিয়াম জেলি দিচ্ছে। মুখে দেয়া তো দিব্যি সম্পূর্ণ ক্রিয়া। কিন্তু ফেয়ার এন্ড লাভলি দেয়া আর সাবান/চন্দন/হলুদ/গ্লিসারিন/তেল দেয়া এক জিনিস না। মুখে দিচ্ছেন/মাখছেন না বলে খাচ্ছেন ক্রিয়াপদই ফেয়ার এন্ড লাভলি মুখে দেয়ার প্রকৃত/সঠিক ক্রিয়াপদ।
এই পযর্ন্ত লেখাজোকার সাথে কবিতার সম্পর্ক খুঁজে পাবো না যতোক্ষণ না আমরা ফেয়ার এন্ড লাভলি সাথে এর পলিটিক্যাল সম্পর্কটি না ভাববো, উত্তর-উপনিবেশিক পাঠ না নিবো, উত্তর-কাঠামোবাদের ছোঁয়া না লাগাবো।
কবিতামুখ শব্দবন্ধ (এখানে শব্দযুগল) নিয়ে এখোন আমরা অন্য আলোচনায় হাঁটবো। আগের আলোচনার রাস্তাটা পরে আবার আমরা ব্যবহার করবো।

চিত্রটি খুব জটিল কিঙবা খুবই সহজ/সরল মনে হতে পারে। তাই এটাকে গম্ভির/ ভেলুয়েবল বানাতে পদার্থবিজ্ঞানের ছোট একটা অধ্যায়ে ঢুকি। সেটা হলো গতিবিদ্যা। এবঙ কয়েকটি ধাপে বিজ্ঞান, চিহ্নবিজ্ঞান, কাব্যতত্ত¡ নিয়ে আলোচনা শেষে আবার ফেয়ার এন্ড লাভলি খেয়ে আলোচনাটি শেষ করবো।
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাথে কবিতার সর্ম্পক
O এখানে একজন কবি। তাকে তার বন্ধু A a বলে এবঙ বন্ধু B b বলে নিজেদের দিকে টানছে। কবি বেচারা A কিঙবা B কোনো দিকেই যেতে না পেরে / না গিয়ে C এর কাছে পৌঁছলো। C এর বল আলাদাভাবে চিন্তা না করে a ও b এর লব্দি হিসেবে চিন্তা করবো। এবঙ একইসাথে দ্বান্দিক বস্তুবাদের সাথে কবিতার সর্ম্পক নিয়ে আলোচনা করবো।

এখোন আমরা একই চিত্র দিয়ে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করবো। সেটা হলো আমাদের সমাজে ক্রিয়াশিল হেজিমনি। এখানেও O একজন কবি। যে A বস্তুটাকে দেখতে চায়। যারফলে তার দৃষ্টি O থেকে A এর দিকে। যার সাধারণ দর্শন A; কিন্তু এখানে B অন্য একটা দর্শন (যা হিজেমনি) কার্যকর থাকায় আমরা A ও B এর লব্দি বরাবর মূলত C বিন্দুতে দেখতে পাবো। A কে আমরা যতোই এক রৈখিক মানে A বরাবর চিন্তা করতে চাইলেও সেটা এক রৈখিক নয়। এবঙ সেটা OC বরাবর (দ্বিরৈখিকভাবে) কাজ করে।

যেমনঃ O বিন্দু থেকে একটি নৌকা A বিন্দুতে পৌঁছার জন্যে a বেগে রওনা হলো। B স্রোত কাজ করায় লোকটি A তে না পৌঁছে মূলত C বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছলো।

অন্য একদিন O বিন্দু থেকে নৌকাটি A বিন্দুতে পৌঁছতে a বেগে এবঙ OA দিক বরাবর না চালিয়ে a ও b এর লব্দি c’ (পিথাগোরাসের সূত্র মতে এটা হবে) বেগে OC’ বরাবর রওনা হলে A তে পৌঁছল।
D নামে অন্য একটা বেগ (ধরে নিতে পারি বাতাসের বেগ) কাজ করলে তার জন্যে নৌকাটি কিন্তু আর D’ বিন্দুতে না পৌঁছে D বিন্দুতে পৌঁছবে। এবঙ একইভাবে দেখা যাবে এ বিন্দুতে পৌঁছতে তাকে C বেগে OC এর দিকে নৌকা চালানোই যথেষ্ট নয়।
কিন্তু স্রোতের বেগ এবঙ বাতাসের বেগ সম্পর্কে না জানা একজন O থেকে যতোই A বিন্দুতে পৌঁছতে চায় কোনো দিনই সে তা পারবে না। এবঙ ক্রিয়াশিল সবগুলো (a, b, c, d কিঙবা আরও কিছু e, f. g… ) সম্পর্কে যার জ্ঞান ও দক্ষতা/ধ্যান থাকবে সে-ই কেবল A তে পৌঁছতে পারবে। নইলে A কে সে C, D, E, F অন্য কোনো রূপে দেখতে পাইবে। এখনেই কাজ করে গ্রামসির হেজিমনি কিঙবা মিশেল ফুকোর ক্ষমতাতত্ত¡ কিঙবা সোস্যুর চিহ্নবিজ্ঞান কিঙবা সুইডেনবার্গের অন্যজগতের দর্শন যেখানে এই জগতের সবকিছুকে অন্যজগতের প্রতিক হিসেবে ধরা হয় এবঙ যেখান থেকেই প্রতিকবাদি আন্দোলনের শুরু) আর এখানেই মূলত কবিতার অবস্থান।
সাধারণভাবে যা a কবির কাছে তা √(a2 + b2) কিঙবা √(a2 + b2 + c2) ইত্যাদি ইত্যাদি
কবিতা = কবি + তা
কবিতা যা কবি তা। কবিতার ভিতরের ইঁটসুড়কি মূলত কবিরই গাঠনিক উপাদান। কথাটার মূল ঠিক রেখে উল্টিয়ে বললে ব্যাপারটা আরো সহজ হবে। যা কবি তা-ই কবিতা। কবির প্রকাশিত (বাস্তববাদ) ও অপ্রকাশিত (মনসমিক্ষণবাদ) উপকরণই কবিতার উপকরণ।
কিন্তু কবি কে? বা কবি কি? কবি মূলত সামাজিক কণা বা অণুসমাজ। রাষ্ট্র এবঙ দেশ শব্দ দুটিতে সমাজ শব্দের রাজনৈতিক বা জাতিয়তাবাদি ফ্লেভার লাগানো। এবঙ আঞ্চলিকতার শব্দমূল হওয়ায় অঞ্চল শব্দটি দিয়ে সমাজকে সম্পূর্ণভাবে (আদতে সম্পূর্ণ বলতে যদিও কিছু নেই) বুঝানো যাচ্ছে না। তাই সমাজই এখোন আমাদের হাতে মোক্ষম শব্দ (ভাষাচিহ্ন)। পাঠকগ্রাহ্যতাতত্তে¡ না গেলেও কবি-কবিতা সম্পর্কের তৃতিয় শব্দটি হলো পাঠক। পাঠকও কবির মতোন অণুসমাজ। এবঙ কবি ও কবিতা শব্দ দুটি অভিন্নার্থ হিসেবে নিচ্ছি।
দু/একটি ভাত টিপলেই হাড়ির খবর বুঝা যায়। অনেকেই হয়তো আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে চাচ্ছেন, না, সবসময় বুঝা যায় না। হতে পারে। কিন্তু পুরোপুরি বুঝা না গেলেও অনেকাঙশে বুঝা যায়।
১. হাঁড়িতে কোন ধরনের/জাতের চাল আছে। অথবা
২. চালগুলো কতোটুকু সিদ্ধ হয়েছে। অথবা
৩. চালের/ভাতের ঘ্রাণ। ভিন্ন জাতের চাল ঢুকে গেলেও ঘ্রাণটা কিন্তু কমন জাতের চালের ঘ্রাণ আসবে। অথবা
৪. চালের রঙ। ঘ্রাণের ক্ষেত্রে রঙও এক। চাল চলের ভিতর সাদা চাল কিঙবা সাদা চালের ভিতর লাল চাল যেরকম হয়। এভাবে চাল (কবি) হাঁড়ির (সমাজ) এর ক্ষুদ্রতম অঙশ।
একজন পাঠক একটা কবিতাকে পড়ে বুঝতে পারলো (অথবা খুঁজে পেলো) কবিতা এটা মূলত A. কিন্তু কবিতাটা কি মূলত-ই A? আমি বলবো কবি ও পাঠকের কমন উপাদান হলো এই A.

এখানে দেখা যাচ্ছে পাঠক হচ্ছে CA টাইপের সমাজের অণুকণা। এবঙ কবি অথবা কবিতা (আলোচনার এই অঙশে আমরা কবি ও কবিতাকে অভিন্নার্থেই দেখছি) AB টাইপ সমাজের অণুকণা। তাই পাঠক কবির B অঙশিদ্বারিত্ব বুঝতে/পাঠ করতে পারছে না। বিপরিতভাবে কবিও পাঠকের C অঙশিদ্বারিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞাত।
কিন্তু একই সাথে CA ও AB টাইপের সমাজ অসম্ভব। এটা মূলত CAB টাইপ (বৃহত সমাজ অর্থেও ধরতে পারি)। এবঙ কারণ তারা একই হেজিমনি প্রভাবিত অণুকণা (গ্রামসি)।

পাঠক ও কবি তাদের ডাবল লাইনঅলা ব্যারিয়ারের জন্যেই পরষ্পরকে পাঠ করতে পারছে না। এই ব্যারিয়ার ভাঙতে পারলে তার বৃহত্তর অঙশ CAB যাপন করতে পারে।

এই বৃহত্তম অঙশ CAB CDF ABP যা-ই হোক না কেনো এগুলো সাধারণ কিছু রেখা /বৈশিষ্ট দিয়ে গঠিত।
১. — রেখা / সরলরেখা (সবকিছুকে সহজভাবে দেখার প্রচলিত র্দশনকেও ধার নিতে পারেন)।
২. ০ বৃত্ত / শূন্য (আপনাকে নির্দিষ্ট কিছুর ভিতওেন থাকতে হবে এই প্রাতিষ্ঠানিকতা কথাই হয়তো এখানে বলা হবে। অথবা যা করেন সব-ই শূন্য। কিছুই কিছু না। সবকিছু ধবঙস হবে কিছুই থাকবে না। আপনাকেও কেমন মরে যেতে হবে)।
৩. ∪ র্অধবৃত্ত / র্অধচন্দ্র / বক্রতা (রেখাঙশে র্অধচন্দ্র র্অধচন্দ্র (মানে গলাধাক্কা) ভাব থাকলেও এটাই মূলত ইন্টারেস্টিঙ থিঙ। র্অধবৃত্ত বললেও এখানে বৃত্তের/ বদ্ধতার কোনো চিহ্নমাত্র নেই। সৃজনশিলতার মূল উপাদান এখানেই সুপ্ত / লুকায়িত। বক্রতা মানে সমাজকে ব্যাকা করে (স্যাটায়ার) দেখার ব্যপারটা এখান থেকেই শিখতে পারি। তবে রেখাটা র্উধমুখি করে এটাকে উম্মুক্ত করতে পারি (মহাবিশ্বের সাথে একিভূত)। আবার নি¤œমুখি কওে এটার ভূমিজ ভাবতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে
A = তিনটি সরলরেখাঙশ
B = একটি সরল, দুইটি র্অধবৃত্ত
C = মাত্র একটি র্অধবৃত্ত
D = একটি সরল একটি র্অধবৃত্ত
E = তিনটি সরল রেখাঙশ। কিন্তু এর সাথে র্পাথক্য হলো এতে কোনো (সিমা)বদ্ধতা নাই।
এইভাবে F থেকে Z অবধি আমাদের সমাজঅঙশ (সামাজিক উপকর) ;

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি, সীমার (জীবাত্মা) মাঝে অসীম (পরমাত্মা) তুমি। কিন্তু সীমার মাঝের অসিম কি অবিকল থাকে নাকি ছিটেফোটা?
সারা জীবন পুকুরে থাকা মাছ আর নদির মাছ এবঙ সমুদ্রের মাছের জিবনযাত্রা এক নয়। পুকুরের মাছে সমুদ্রের মাছের আচরণ খুঁজতে গেলে র্ব্যথ হতে হবে যেমন পুকুরের ঢেউ (যেটাকে আমরা পানির সাধারণ আলোরণও বলতে পারি) আর নদির ঢেউ এবঙ সমুদ্রের ঢেউ।
বক্রোক্তি জীবিতং
প্রসিদ্ধং মার্গ মুত্সৃজ্য যত্র বৈচিত্র্যসিদ্বয়ে।
অন্যথৈবোচ্যতে সার্হগঃ সা বক্রোক্তি রুদাহৃতা।।
বক্রোক্তিজীবিতং গ্রন্থের লেখক কুন্তকের বক্রোক্তি মতবাদকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর্চায মহিম ভট্ট ঘোষণা করেন, যেখানে বৈচিত্র উতপাদনের (সিদ্ধির) জন্যে স্বাভাবিক (প্রসিদ্ধ) পথ (র্অথ) পরিত্যাগ কওে ভিন্ন র্অথ গ্রহন করা (অন্য প্রকার উক্ত হয়) সেই র্অথকেই বক্রোক্তি বলে।
কুন্তকের মতে কাব্যনির্মাণ রস দিয়ে হয় না। হয় কথা বা উক্তি দিয়ে অর্থাত বক্রোক্তির সাহায্যে।
বক্রভাবঃ প্রকরণে প্রবন্ধেবাস্তি সাদৃশ্যঃ
উচ্যতে সহজার্হায সৌকুর্মায মনোহরঃ
অর্থাত এর সারতসার হচ্ছে কোনো বিশেষ অঙশ নয়। সমগ্র রচনায়ই বক্রতাব্যাপ্ত এবঙ সমগ্র নাটক-প্রবন্ধের মূল চারুত্ব ও মানোহরিত্বই বক্রভাব বা বিন্যাস বৈচিত্র।
ভরত থেকে শুরু করে অভিনবগুপ্ত যেখানে শব্দ অর্থ অলঙ্কারকে কাব্যতত্ত্বের মূল হিসেবে দেখছে কুন্তক সেখানে বক্রোক্তিকে কাব্যতত্ত্বের মূল হিসেবে দেখছে। কুন্তকের মতে প্রতিভাহিন কবিগন শুধুমাত্র শব্দের মাধুর্য়ের দ্বারা অর্থের চাতুর্যের মাধ্যমে কবিতা সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু র্সাথক কবিতা এভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। শব্দ ও অর্থ মিলে তার চমতকারিত্বে কবিতা সৃষ্টি হয়। তবে এই শব্দার্থের বিশিষ্টতা থাকতে হবে। এই বিশিষ্টতাই বক্রোক্তি।
সাহিত্যম্ অনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতিকাব্যসো।
অন্যূনানতিরিক্তত্ব মনোহরিণ্য বস্তিতিঃ।।
(বক্রোক্তি-জীবিতং)
সাহিত্য হচ্ছে এদের; অর্থাত শব্দযুগলের এক অলৌকিক / চমতকারিত্ব বিন্যাসভঙি যা ন্যূনতা ও অতিরিক্ততা বর্জিত হয়ে মনোহারি হয় এবঙ শোভাশালিতা প্রাপ্ত হয়।
তারপর শর্ব্দাথ যুগলের অলৌকিক বিন্যাসভঙি বুঝাতে গিয়ে বলে
শব্দাথৌ সাহিতৌ বক্রকবিব্যাপরশালিনি।
বন্ধে ব্যবস্তিতৌ কাব্যং তদিদাহাদ কাবিনি।।
(বক্রোক্তি-জীবিতং)
মিলিত শব্দার্থযুগল কাব্যজ্ঞগনের আতাদজনক বক্রতাময় কবিব্যাপারর্পূণ রচনাবন্ধে বিন্যস্ত হলে কবিতা হয়ে থাকে। তবে রসবাদি বা ধ্বনিবাদি আলংকারিকরা কুন্তকের বক্রোক্তিবাদকে মেনে নিতে পারেনি।
সবকিছু মূলত স্যাটায়ারে রূপ নিয়েছে
এই শব্দটা কাব্যিক। ওই শব্দটা কাব্যিক না। এরকম মতামতের সাথে আমার অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিমত নাই। কিন্তু কবিতায় একমাত্র কাব্যিক শব্দই স্থান পাবে এ মতে আমি তিরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। কবিতায় আমি সর্বেশ্বরবাদি। আযান থেকে আঘ্রাণ বরবটি থেকে কলা যেকোনোটিই কবিতার শব্দ হতে পারে। এমনকি কবরিকলা থেকে আঁটিকলা সবই কবিতাকলার উপাদান। এটা সত্য সব আঙিকে সব শব্দ সবক্ষেতে মানানসই হয় না। এক্ষেত্রে বিষয় আঙিক গল্প কিঙবা চিত্রকল্পের বিভিন্নতার জন্য শব্দবাছাইকরন র্নিভর করবে।
যেহেতু এখানে কবিতাকে কবির অভিন্ন হিসেবে দেখছি এবঙ কবিকে দেখা হচ্ছে অনুসমাজ হিসেবে তাই আজকে আমরা সমাজ (যেখানে সময় প্রযুক্তি রাষ্ট্র জাতিয়তা / দেশ) নিয়ে বিশ্লেষণে যাবো।
এখোন আমরা দৈনন্দিন কিছু ঘটনা / দৃশকে উপস্থাপন করবো।
১। কয়েকজন কবি স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত কিঙবা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবঙ অনুপ্রাস অন্তমিল নিয়ে মাথা ফাটাফাটিরকম র্তক করতে করতে নড়বড়ে বাসের ঝাকুনিসহ ভাঙারাস্তার ঠ্যাকনা খেতে খেতে কোনো এক শাহবাগের দিকে এগুচ্ছে।
২। গ্যাস্ট্রিক আলসালে আক্রান্ত সারারাত নাঘুমানো একজন সকালে যখোন বিশেণজ্ঞ ডাক্তারের খোঁজে বের হচ্ছেন রাস্তায় তার পরিচিত একজন
আসসালামুআলাইকুম ভাই
ওয়ালাইকুম আসসালাম।
কেমন আছেন
ভালো।
৩। মগবাজার ফ্লাইওভারের পিলারে সরকার দলিয় পোস্টার লাগানো হয় গতরাতে। আজ সকালে তার উপর লাগানো হলো সিনেমার পোস্টার। তারসাথে মহাসমারোহে সারাদেশে চলিতেছে লেখা ছোট্টআকারের পোস্টারটি। সন্ধ্যায় রাস্তায় ঘুমানোর জন্যে সিনেমার পোস্টারটি তুলো ঘুমিয়ে রইলো। সকালে দেখা গেলো সরকার দলিয় নেতাদের হাসিহাসি খুনিখুনি চেহারার উপর লেগে আছে মহসমারোহে সারাদেশে চলিতেছে পোস্টারটুকরা।
৪। নৌকায় ভরসা রাখুন স্লোগানটি যখোন রাজারবাগ রাস্তার থৈ থৈ করা পানির উপর নৌকার চালানো কোনো ফটোগ্রাফের ক্যাপসান হয়।
৫। কিঙবা জাতিয় শোক দিবস উপলক্ষে ঘারমোড়া ক্লাবের টিভিতে কোনো এক বক্তা টকশোর টেবিল গরম করে বঙ্গবন্ধুকে যখোন প্রথম রাষ্ট্রপতিত্ব এবঙ তিন বছর প্রধানমন্ত্রিত্ব করার কথা বলছিলো বাইরের মাইকে জোড়ে জেড়ে তখোন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ: আমি আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।
রাজনিতিক থেকে শুরু করে প্রায় সবার কথা/কাজ এই রকম যে একজন সানি লিয়ন কথায় কথায় যদি বলতে থাকে আমি যেহেতু কুমারি আমি যেহেতু কুমারি। এভাবে হাজার হাজার ঘটনার মধ্যে দিয়ে সবকিছু মূলত স্যাটায়ারে (বক্রতায়) রূপ নিয়েছে। তবে বক্রোক্তিবাদ/তত্ত¡ শুধু স্যাটায়ারই প্রকাশ করে না। ব্যঞ্জনার অন্য অঙশও প্রকাশ করে।
সাহিত্য/কবিতায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োগ হিসেবে পাশাপাশি দুইটা বস্তু (বস্তুভাব, বস্তুর ক্রিয়াও এর অর্ন্তভূক্ত) দাঁড় করাতে পারি। আর সহজ করে বলতে গেলে দুইটি ছবি বিবেচনা করতে পারি।
১। হতে পারে চিত্রকল্প,
২। ঘটনা, যা বর্ণনার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পাওে,
৩। সঙলাপ, যা কথোপথনের লিখিত রূপ,
৪। শব্দ, যারা পাশাপাশি বসে ভিন্ন অর্থের দিকে নিয়ে যায়।
এটা ওয়ান-ওয়ান বা টু-ওয়ান বা টু-টু সমন্বয়েও হতে পারে।

আমরা এখোন আলাপ করবো বস্তুমূল দর্শনের এবঙ প্রকাশে কবির সিমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে। এজন্যে আমাকে আবারও গতিবিদ্যার পাঠ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

সাধারণ দর্শন = বস্তুর চিহ্ন a
কবির দর্শন = বস্তুর চিহ্ন √(a2+b2)
কবি কোনো শব্দ তৈরি করতে পারে না। শব্দকে প্রতিক উপমা দ্বিরুক্তি হিসেবে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে শব্দকে উন্নত করতে পারে। বিভিন্ন ভাষা/ভাষাঅঞ্চল থেকে শব্দকে ব্যবহার করার কাজ সে করলেও কোনো শব্দ/চিহ্ন তারা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু সোস্যুরের তত্ত্ব অনুযায়ি শব্দ/চিহ্ন এখানে মূলবস্তু সর্ম্পূণ প্রকাশে অক্ষম (শুধুমাত্র একটা ধারণাই দিতে পারে)।
চিহ্ন/শব্দের এই অসম্পূর্ণতা/অক্ষমতাই কবির জন্য সুযোগ। এই সম্পূর্ণ চিহ্নের সাথে অন্যান্য চিহ্ন যোগ করে দূশ্যমান বস্তুকে প্রকাশ করার ক্ষমতাই কবির ক্ষমতা। একজন চিত্রশিল্পির রেখা/রঙেও সেই একই সিমাবদ্ধতা এবঙ একজন সঙিতজ্ঞের সুরেও (মিউজিক/সাউন্ড) একই সিমাবদ্ধতা দেখা দেয়। এই সিমাবদ্ধতাকেই সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়ে কবিকে কবি শিল্পিকে শিল্পি হতে হয়।

তাই কবির / শিল্পির কাজ দ্বিগুণ হয়ে উঠে (কুন্তক এর বক্রতাবাদ তা-ই বলে)
১। এই জগতের বস্ত্ত দেখে অন্যজগত/ প্রকৃতজগতের বস্ত্তমূলকে র্দশন করা/ দেখতে পারা।
২। দৃশ্যমান বস্তুকে সিমাবদ্ধ চিহ্ন / রেখা / সাউন্ড দ্বারা র্পূণরূপে উপস্থাপন করা।

গণিতকে যেভাবে বিজ্ঞানের মেরুদন্ড বলা হয় কবিতাও আমাদের কাছে সাহিত্যের মেরুদন্ড। এই কবিতাকে ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে থাকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলো (গল্প নাটক সমালোচনা)। একইভাবে কবিতার ভিতওে বাস করে একেকটা গল্প একেকটা নাটক। আলোচনার সুবিধার্থে কবিতাকে আমি ভিন্ন প্রকরণে ফেলবো।
১। শব্দিক কবিতা
২। বাক্যিক কবিতা
৩। গাল্পিক কবিতা
৪। দৃশ্যিক কবিতা

রলাঁ বার্ত সাহিত্যকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে সাহিত্য কেবল বস্তুর র্অথ নয়, র্অথ উতপত্তির বার্তাও (সিগনিফিক্যাশান): সিগ্নিফিকেশন শব্দটির দ্বারা সেই প্রক্রিয়াটির কথা বলতে চেয়েছেন, যা নানান র্অথকে জন্ম দেয়, নির্দিষ্ট কোনো একটি র্অথকে নয়। বারেÍর মতে একজন সাহিত্যিকের সব চাইতে বড় অপরাধ হলো যখোন তিনি পাঠককে এই বলে পথভ্রষ্ট করেন যে ভাষা একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ মাধ্যম যার দ্বারা সত্য বা বাস্তবের যথাযথ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
শব্দই ব্রহ্ম জ্ঞান করে প্রথম আমরা শব্দ/চিহ্নর দিকে হাঁটবো। আম জাম কলা লিচু এসব চিহ্নের কোনটিই তার বস্তুর সাথে সম্পর্কিত নয়। আকারে/প্রকারে কোনোভাবেই না।

এই শব্দগুলো মিথ / মিথ্যা / আরোপ করে একে শক্তিশালি করা হয়েছে এবঙ নির্দিষ্ট বস্তুকে প্রকাশ/চিহ্নিত করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এই জন্যে যেকোনো চিহ্ন / শব্দই রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন। ঈশ্বর থেকে শিয়াল সব চিহ্নের মধ্যেই এই ক্ষমতা। এই ক্ষমতা এসেছে অনেকগুলো অঞ্চল থেকে:
১। রাজনিতি
২। সমাজ
৩। ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান
৪। জেনডার / সেক্স
৫। ভাষা / ভাষা অঞ্চল
৬। জাতি এবঙ আরও অনেকগুলো।
দর্শক ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ কি কি চিন্তা করছে?

চিহ্ন বিদ্যা অনুযায়ি এগুলোর কোনোটাই দূরবল কিঙবা সবল হবে অঞ্চল ভেদে। মানে রাজনৈতিক সমাজ কিঙবা জেন্ডার প্রভৃতির উপর র্নিভরশিল এদের র্অথ।
এটা হলো একই বস্তু/সিগনিফাইড এর বিভিন্ন চিহ্নয়ক/সিগনিফাইয়ার । এখোন আমরা একই সিগনিফাইয়ারের বিভিন্ন র্অথ/বার্গাথ নিয়ে আলোচনায় ঢুকবো।
পানিণির বার্গাথ বিদ্যা যা পরে সোস্যুর ডেভলাপ করে সেটা হলো, প্রত্যেক চিহ্নের/শব্দের অনেকগুলো লক্ষণা থাকে কিন্তু আভিধানিক র্অথ থাকে মাত্র একটি/মাঝে মাঝে এশাধিক। মাথা হেড এর আভিধানিক র্অথ দেহের গুরুত্বর্পূণ অঙশ যেখানে মস্তক থাকে। কিন্তু মাথার লক্ষণাগুলো হচ্ছে প্রান্ত চূঁড়া প্রধান মূল কেন্দ্র জ্ঞান ইত্যাদি। এই চিহ্নটি/মাথা তখোনই ব্যঞ্জনা তৈরি করতে পারবে যখোন এটি আভিধানিক কিঙবা লক্ষণা অর্থে ব্যবহার হবে না। এবঙ চিহ্নের এই ভিন্ন উপায়ের ব্যবহারের মাধ্যমেই বক্রোক্তি তৈরি হয়। ভারতিয় কাব্যতত্ত্বে যা গুরুত্বর্পূণ স্থান দখল করে আছে।
বক্রোক্তি হিসেবে ব্যঞ্জনা তৈরির মাধ্যমে যে খোচা তৈরি করা হয় তা-ই হলো স্যাটায়ার।

অভিধা: মাথায় হাত দিয়ে মা আমাকে আশির্বাদ করছে।
লক্ষণা: রাস্তার মাথায়ই আমাদের বাড়ি।
ব্যঞ্জনা: তোমার আসকারায় ছেলেটা মাথায় উঠেছে।
অভিধা ও লক্ষণা হলো ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু ব্যঞ্জনা হলো নন্দনতত্ত্বের অধ্যায়। আগেই আলোচনা করা হয়েছে কবি কোন শব্দ / চিহ্ন তৈরি করতে না পারলেও দুই/ ততোধিক শব্দ যুক্ত করে নতুন র্অথ / ব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে পারে।

আকাশকুসুম অশ্বডিম্ব এরকম অনেক শব্দযুগল এক সময় নন্দনতত্ত্বের/ব্যঞ্জনার অঙশ হলেও ব্যবহারে দিনে দিনে ব্যকরনের ভিতর আশ্রয় নিয়েছে।
আসুন আমরা হাতুরির গান শুনি
রাস্তায় অফিসে বাসে ট্রেনে পার্কে বাড়িতে যেখানেই যাই সবকিছু কেমন স্যাটায়ার স্যাটায়ার লাগে। এই যে গণতন্ত্র কিঙবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে শুরু করে দুনীতি দমন কমিশন কিঙবা মানবাধিকার কমিশন সবকিছুই স্যাটায়ার বহন করে। অনলাইন থেকে অফলাইন ছবি ভিডিও সঙলাপ শব্দ সবই আজ স্যাটায়ারে আশ্রয় নিয়েছে। মালিবাগের রাস্তায় থৈ থৈ পানি, ছবির নিচে লিখে দিলো উন্নয়নের বন্যা / জোয়ার। অথবা ধুলায় ঘোলাটে হয়ে গেছে যাত্রাবাড়ির মোড়, ছবির নিচে লিখে দিলেন পরিবেশ বান্ধব ধুলাবালি।
অনেক প্রতিবাদি কথার চেয়ে একটিমাত্র শব্দ দিয়ে একটা বিষয়কে খোঁচা মারা বা আঘাত করার ক্ষমতা স্যাটায়ার ছাড়া আর কোন ফরমের আছে!
এখানে আমরা আলোচনা করবো শব্দযুগল কিকরে ব্যঞ্জনা থেকে স্যাটায়ারে রূপান্তরিত হয়। AB শব্দযুগলের একটি যদি অন্যটিকে
১. আঘাত করে
২. বিরোধিতা করে
৩. এমোনকি অসৃকার করে
তবেই সেই শব্দযুগল স্যাটায়ার তৈরি করতে পারে। প্রতিদিন হাগাহাগি করলেও গু শব্দ আমাদের মুখ দিয়ে বের হয় না। কেউ গু উচ্চারণ করলে শালিনতায় / সুশিলতায় / ভদ্রতায় / আধুনিকতায় / সামাজিকতায় এটাকে গ্রহনযোগ বলে মেনে নেয় না। সুলিশ ভদ্র শিক্ষিত আধুনিক এই শব্দগুলোর সাথে গু যুক্ত করে দিলেই তাই স্যাটায়ার তৈরি হয়। কিন্তু এটাকে আমরা শাব্দিক স্যাটায়ারই হিসেবেই দেখবো।

এখোন আপনার র্স্মাটফোনের গুগোল প্লেস্টোরে সাউন্ড মিটার কিবঙা ডেসিমিটার ডাউনলোড করতে পারেন। কোনো একটা কন্সট্রাকশন সাইটে কিঙবা ওর্য়াকশপে গিয়ে ড্রিল করার কনটিনিউয়াস নয়েজের / সাউন্ডের সামনে ধরলে সাউন্ডমিটারের গ্রাফটি আর হেমারিঙ এর সামনে ধরলে তার গ্রাফটি তুলনা করতে পারেন।

মরিচা পড়া একটা পেরেকের উপর এককেজির একটা বাটখারা চেপে ধরলেই কি পেরেক থেকে মরিচাটা ঝরে পড়ে? আপনার উত্তর হবে নিশ্চিত, না। যদি বাটখারাটি দুই কেজি হয়? না। পাঁচ কেজি? তা-ও না। কিন্তু ৫০০গ্রামের একটা বাটখার দিয়ে হেমারিঙ করলে নিমিষেই মরিচাটা ঝরে পড়ে। মরিচা ঝরাতে চাইলে এই কনটিনিউয়াস আঘাতের চেয়ে থেমে থেমে এবঙ কিছুটা দূর থেকে আঘাত করাটাই র্কাযকরি পদক্ষেপ।
এই ইমপেক্ট সাউন্ড গ্রাফটি হলো স্যাটায়ার কবিতার মূলশক্তি। নির্দিষ্ট / র্নিধারিত বিষয় / দৃশ্যকে তার বিরোধি চিন্তার (যা কবির দর্শনঅস্ত্র) বিষয় / দৃশ্য / শব্দ দিয়ে বারেবারে এবঙ বিভিন্ন দিক থেকে আঘাতের মাধ্যমে (বিভিন্ন আঙিকে আঘাত করতে পারলে ) স্যাটায়ারে রূপ নেয়।


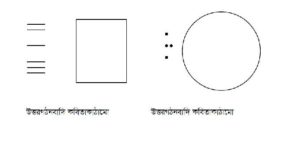
কোনো শব্দকে স্যাটায়ার করতে গেলে অবশ্যই কেমিক্যাল রিয়েকশান তৈরি করতে হয়। যেটা এবি শব্দযুগলের আলোচনা করার সময় বলা হলো। সেখানে প্রথম শব্দটিকে (মূলত শব্দের র্অথটিকে ) খোঁচা / বিদ্রুপ করতে পারে এমোন অন্য একটি শব্দ দিয়ে স্যাটায়ার করা হয়। স্যাটায়ার করা শব্দটি (অথবা শব্দাঙশটি) আগে হলেও স্যাটায়ার তৈরি হয়। কিন্তু আগের কৌশলের চেয়ে পরের কৌশলটি বেশি জোড়ালো হয়। তবে দুইভাবেই শব্দযুগলের (শব্দের কেমিক্যাল রিয়েকশান করে) স্যাটায়ার তৈরি সম্ভব।


মিথ (অথবা মিথ্যা)-ই শব্দকে প্রাণ দেয়
ফেয়ার এন্ড লাভলী ১৯৭১ সালে ইউনিলিভার ইনডিয়ার মাধ্যমে জন্ম হঔের এর ইতিহাস কয়েক হাজার বছর পুরনো: উপনিবেশিক ইতিহাসের সমান। র্আয থেকে বৃটিশ এবঙ হালআমলের কালচারাল কলোনিয়ালিজমের যুগে ফেয়ার হলেই শুধু মাত্র তা লাভলি হয়। তাই বলেই সাদা মনের মানুষের খোঁজে তন্যতন্য খুঁজে মরছে কবি থেকে কসাই সবাই।
রানা নামের একটা ছেলে আমার যাওয়াআসা আছে এমন একটা এলাকায় চাঁদাবাজি করে বেড়ায়। তার বাবা সরকারি দলের হোমড়াচোমড়া। রানা তার বাবাকে নিয়ে অনেক প্রাউড, তার বাবা এইটা তার বাবা ওইটা, কি না! ফেসবুকে অনেক ছবি ছড়ানো। বাবা মা তার ছোটোবেলার ছবি।
সবার কাছেই সবার বাবা মূলত নায়ক। কিন্তু একদিন রানা জানতে পারলো তার বাবা তার মাকে র্ধষণের পরে তার জন্ম এবঙ তখোনও তার বাবার দল ক্ষমতায় ছিলো। তার মা ও তাকে মেনে নেয়নি। কিন্তু আলাদা করে ভাড়া করে রাখতো।
এখোন রানা চাঁদাবাজি তো দূরের কথা কারো সাথে জোড়ে কথাও বলে না। তার কাছে তার বাবা শব্দটা ব্যক্তিটা মায়ের সাথে তার সাথে বাবার ছবিগুলো কেমোন লাগবে! সেই এক-ই অর্থ প্রকাশ করবে?
ব্লাক ডগ অথবা ইয়েলো মানকি বলে তাচ্ছিল্য করার মানসিকতা (উপনিবেশিকতা) থেকেই ফেয়ার এন্ড লাভলির জন্ম। এবঙ একই ইতিহাস থেকে বিবরতিত (মিথলজিক্যাল) হয়ে সাদা শব্দের র্অথ দাঁড়ায়, সুন্দর সভ্য মঙ্গলময় পরিস্কার। আর কালো মানে, ময়লা কুতসিত অসভ্য নোঙরা অপরিস্কার অন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্খ অপরাধি দুর্নিতিবাজ। পেতিকবিদের উদাহরণ কি দিবো, গুরুকবি রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম না। সুলেখা কালি। কলঙ্কের চেয়েও কালো। (অনেকেই হয়তো কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, বলে আমাকে থামিয়ে দিতে চাইবেন। আমি বলবো এটাই রবীন্দ্রনাথ। এক দ্বিধান্বিত রবীন্দ্রনাথ।)
কিন্তু আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি, রুখে দাঁড়িয়েছি। ভুপেনের কৃষ্ণবরণ আফ্রিকা মোর কৃষ্ণকলি মা, কফিল আহমেদের আফ্রিকা আফ্রিকা, কৃষ্ণকলি ইসলামের নাচো তো কালি গানগুলো আমাদের রুখে ফেয়ার এন্ড লাভলী মানসিকতাকে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগাবে।
শব্দ যেখানে মিথের সঙযোগেই অর্থ হয়ে দাঁড়ায়, সে অর্থটা মূলত রাজনৈতিক/ মিথলজিক্যাল। তার কোনো শব্দের / শব্দের অনেক বিবরতন না জানলে এর স্যাটায়ারটা বুঝা সহজ না। মাউনব্যাটনের ঐতিহাসিক ঘটনা না জানলে হেমাঙ্গ বিশাসের মাউনব্যাটন মঙ্গলকাব্যের স্যাটায়ার বুঝা কি সম্ভব?
একদিন যে বাবা জানার পরে সে মায়ের ধর্ষক। তখোন মায়ের পাশের ধর্ষকের ছবি দেখে তার কাছে স্যাটায়ার / খোঁচা না লেগে পারে না।